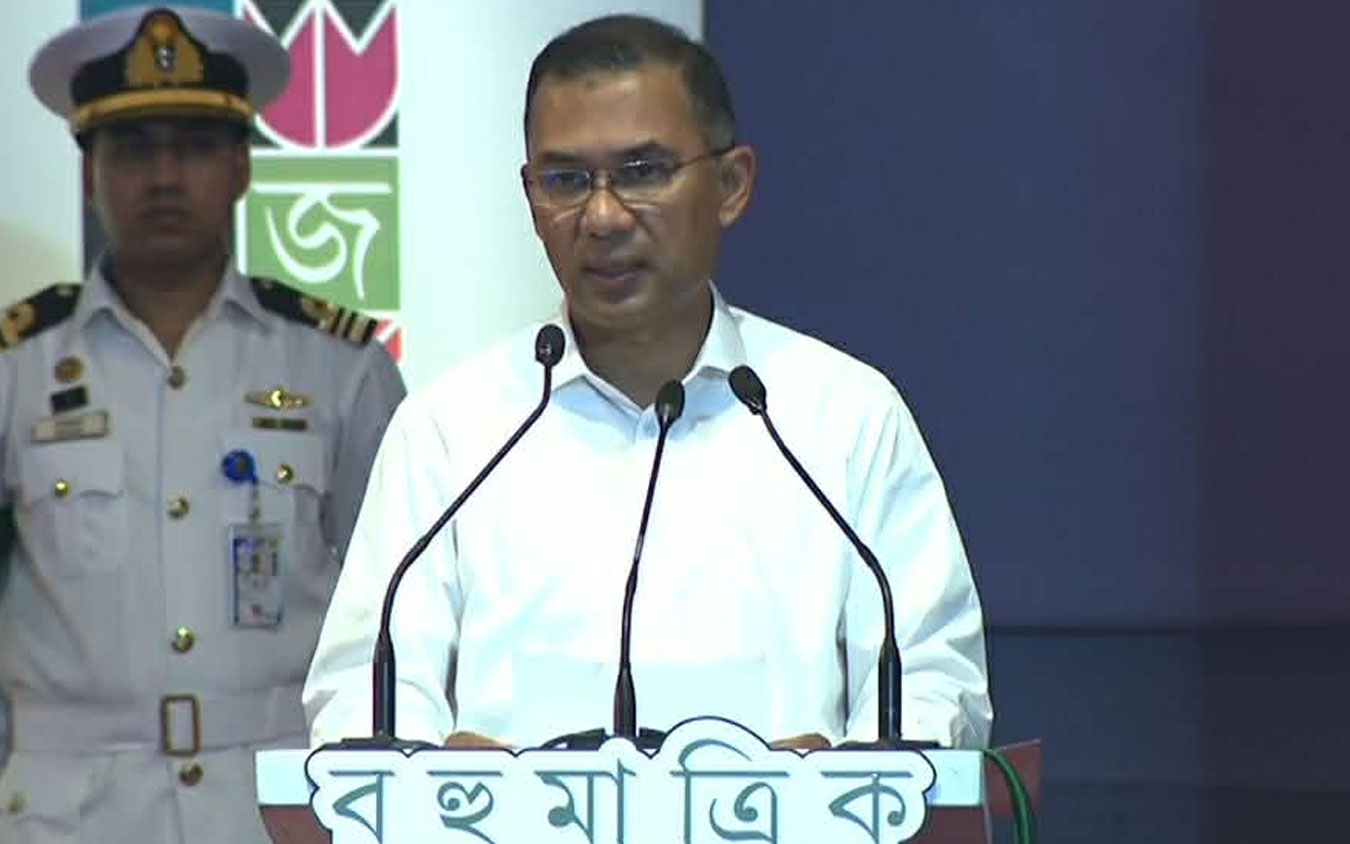আগামী অক্টোবরেই বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে যাচ্ছে বহুল আলোচিত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বহুল আলোচিত এই বিদ্যুৎকেন্দ্র। বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) প্রকল্প পরিচালক সুভাস চন্দ্র পান্ডে এমন তথ্য জানিয়েছেন।
বাগেরহাটের রামপালে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে নবনির্মিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির দাপ্তরিক নাম বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড সংক্ষেপে (বিআইএফপিসিএল)। তবে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নামেই পরিচিতি পেয়েছে স্থাপনাটি। প্রকল্প পরিচালক সুভাস চন্দ্র পান্ডে জানান, গত ১৫ অগাস্ট ৯১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমরা লোড দিয়েছি। ধারাবাহিকভাবে তা বাড়িয়ে সক্ষমতা যাচাই করব। আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী অক্টোবরের শেষ নাগাদ খুলনা অঞ্চলের জন্য ইউনিট-১ এর মাধ্যমে একটি লাইনে ৬৬০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারব।রামপালে আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় আসতে পারে বলে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।
তারা বলছেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ওই সফরেই দুই দেশের সরকার প্রধান ‘বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সুপার থারমাল বিদ্যুৎকেন্দ্র’টির বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারেন। খুলনা অঞ্চলের জন্য বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন নির্মাণও শেষ হয়েছে। জাতীয় গ্রিড সংযুক্ত করা হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির সঙ্গে। সঞ্চালন লাইনটির জন্য নির্মিত সুইচবোর্ড এখন পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহার করছে বলে জানান সুভাস পান্ডে। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আসা উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় খুলনা অঞ্চল। সেজন্য রামপালের সুইচ বোর্ড ব্যবহার করে ভোল্টেজ কমিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।
এছাড়া রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্মিত এ সুইচবোর্ড জাতীয় গ্রিডও ব্যবহার করছে, যা একটি বড় ধরনের সুবিধা বলেও মনে করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। সরেজমিনে দেখা যায়, দুটি ইউনিটের মাধ্যমে দুটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। এর মধ্যে ইউনিট-১ খুলনা অঞ্চলের জন্য, যেটি আগামী অক্টোবরেই পুরোদমে উৎপাদনে যাচ্ছে। আর ইউনিট-২ উৎপাদনে যাবে আগামী বছরের মার্চে। ইউনিট-২ উৎপাদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পুরো সক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। পুরো প্রকল্পের প্রস্তুতি ৮২ দশমিক ২৫ শতাংশ শেষ হয়েছে বলে জানান প্রকল্প কর্মকর্তারা।
রামপালের পশুর নদীর তীরে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। বয়লার ঠাণ্ডা ও উচ্চ চাপ তৈরি করতে এ নদী থেকেই প্রতিদিন পানি সংগ্রহ করা হবে। আর বিদ্যুৎ তৈরির প্রধান কাঁচামাল হবে আমদানি করা কয়লা। রামপালে স্থাপিত কেন্দ্রটিতে দেশীয় কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর নয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশেষ গ্রেডের কয়লা আমদানি করতে হবে ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকার দেশ বা মোজাম্বিক থেকে। এখন ইন্দোনেশিয়ার কয়লা ব্যবহার করেই ট্রায়াল উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। এজন্য এক পাশে নদীর তীরে জেটি নির্মাণ করা হয়েছে, যা বিদুৎকেন্দ্রটির জন্য বরাদ্দ দেওয়া ৯১৫ একর জমির সীমানাধীন। জেটি থেকে উচ্চ ক্রেইনের মাধ্যমে কয়লা সরাসরি কনভেয়ার বেল্টে করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের বয়লার ও চারটি শেডে চলে যায়। প্রতিটি কয়লা ‘শেডের’ মজুদ সক্ষমতা আড়াই লাখ মেট্রিক টন। চারটিতে মোট ১০ লাখ টন কয়লা মজুদ করে রাখা সম্ভব হবে।

এ পরিমাণ কয়লা দিয়ে তিন মাস বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব বলে জানান কর্মকর্তারা। সুভাস পান্ডে আরো জানান, প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৫০ গ্রাম কয়লা লাগবে, যদি সর্বোচ্চ সক্ষমতা ব্যবহার করা হয়। তার ভাষ্যে, পুরোদমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে প্ল্যান্টের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করার সময় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ পরিমাণ কয়লা লাগবে। আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে কয়লার ব্যবহার। কেন্দ্রটি শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেবে। আর বিতরণ পর্যায়ে দাম কত হবে, তা নির্ধারণ করবে সরকার। তবে এই কেন্দ্রের বিদ্যুতের দাম কয়লার দরের উপর নির্ভর করবে জানিয়ে সুভাস পান্ডে বলেন, এটি কারও হাতে নেই। বিশ্ববাজারে কয়লার দাম কেমন হবে, তা সময় বলতে পারবে।
খবর নিয়ে জানা যায়, যে গ্রেডের কয়লা রামপালে প্রয়োজন, প্রায় এক দশক আগে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ শুরুর সময় ইন্দোনেশিয়ায় তার দর ছিল প্রতি টন ৮০ ডলার; এখন তা ১৫০ ডলারে ছুঁয়েছে। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের পাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের বিরোধিতা শুরু থেকেই করে আসছেন পরিবেশবাদীরা, জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কোও এনিয়ে তুলেছিল আপত্তি। বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে ব্যবহৃত কয়লায় তাপ সৃষ্টি ও বাতাস, জাহাজ চলাচল, নদীর পানি দূষণের শিকার হয়ে সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করে আসছেন পরিবেশবাদীরা।তবে পরিবেশের ক্ষতি ন্যূনতম মাত্রায় রেখেই এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান, এখানে ধোঁয়া নির্গমনে ২৭৫ মিটার উচ্চতার চিমনি ব্যবহার করা হচ্ছে। আর সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে, যেন পরিবেশের উপর ঝুঁকির মাত্রা সর্বনিম্ন থাকে। এছাড়া বাতাসে ধোঁয়া ছাড়ার আগে এফজিডি (দ্য ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন) সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে।
সুভাস পান্ডে বলেন, এর মাধ্যমে বয়লার থেকে বের হওয়া ক্ষতিকর সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস আর বাইরে যাবে না। তা পিউরিফাই (পরিশোধন) হয়ে চিমনির বাইরে বের হয়ে বাতাসে মিশবে, যা বাতাসকে দূষণ করবে না। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। বিদুৎকেন্দ্র ব্যবহৃত হওয়ার পর গরম পানি পশুর নদীতে ফেলার আগে ঠাণ্ডা করা হবে, যাতে নদীর পানির গুণাগুণ অক্ষত থাকে।
১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ১৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি দিচ্ছে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা করে। বাকি অর্থের জোগান হচ্ছে ভারতের এক্সিম ব্যাংক। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ভারতের ঋণে চারটি এলওসির বিপরীতে ৭৮৬ কোটি ডলারের ৪২টি প্রকল্প নিয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি সম্পন্ন হয়েছে।
বিজনেস বাংলাদেশ/হাবিব